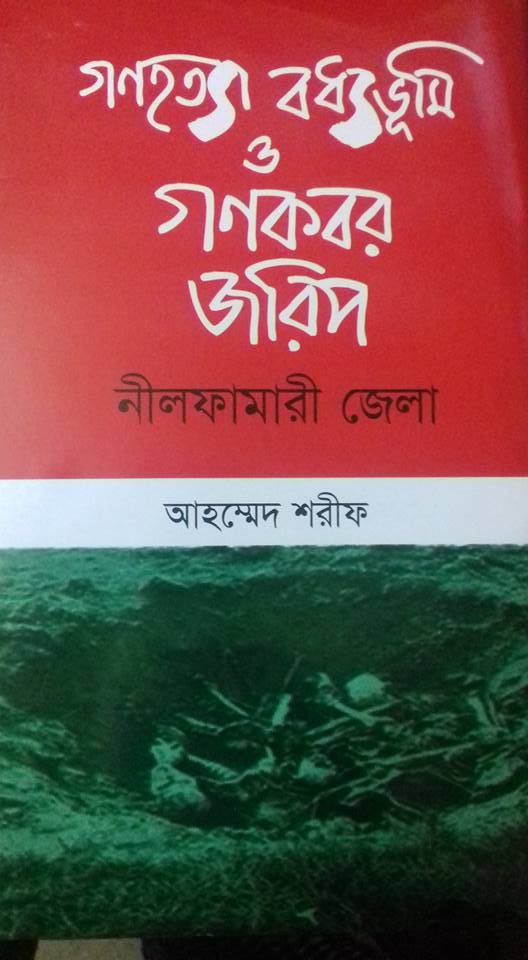গণতন্ত্র বলতে বুঝায় শাসন প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণে জনগণের মতামতের প্রতিফলন। সকলের জন্য সমান অধিকারের বুলি আওড়িয়েই গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।
এই গণতন্ত্রের সাথে কোটা ব্যবস্থা সাংঘর্ষিক। এটা স্পষ্টত বৈষম্য। তবে বৈষম্য সবসময় নেতিবাচক হয় না। পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টিকে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোটা প্রথা বিদ্যমান, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় ইতিবাচক বৈষম্য। অর্থাৎ বৈষম্য দূরিকরণের লক্ষ্যে বৈষম্য। এতে দেশের আপামর জনগনের সমর্থন থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ এর (১) এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। সংবিধানে কোটা শব্দটা না থাকলেও ২৯ এর (৩) এ কথার মারপ্যাচে কোটা ব্যবস্থাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।
তবে সেখানে তিন শ্রণির লোকের জন্য কোটার কথা বলা হয়েছে–
১. সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য;
২. ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ের তাঁদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিষয়ে;
৩. কাজের ধরণ ও উপযুক্ততা বিবেচনায় নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে।
বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে ৫৬% কোটার কথা বলা আছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০%, নারী ও জেলা কোটা ১০ % করে, ৫% কোটা রাখা হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য, আর প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে ১% কোটা। বাকি ৪৪% মেধা কোটায় বরাদ্দ।
প্রতিবন্ধী কোটার বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত থাকার কথা না। সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণি হিসাবে তাঁরাই কোটার মূল দাবিদার। ১৯৯৭ সালে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা চালু করা হয়। ১৯৭২ সালে জেলা ছিল ১৮ টি। আঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে জেলা কোটা চালু করা হয়। সে সময় প্রথম শ্রেণির চাকরিতে জেলা কোটা ছিল ৪০%। পরে ১৯৭৬ সালে ৩০% এবং ১৯৮৫ সালে ১০% এ নামিয়ে আনা হয়। জেলা কোটা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা পরিষ্কার না।
অনেকে মনে করে থাকেন শুধু অনুন্নত জেলাগুলোর জন্য জেলা কোটা, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। দেশের ৬৪টা জেলার জন্যই কোটা রয়েছে। একটু পরিষ্কার করে বলি– জেলা কোটা নির্ধারণ করা হয় জনসংখ্যার অনুপাতে। যে জেলার জনসংখ্যা যত বেশি তার কোটার হারও বেশি। ঢাকা জেলার জনগণ সর্বোচ্চ ৮.৩৬ % এবং বান্দরবান জেলার মানুষ সব থেকে কম ০.২৭ শতাংশ কোটা পাবেন। এই প্রক্রিয়ায় ছোট জেলাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সুতরাং জেলা কোটা বাতিল এখন সময়ের দাবি। তবে দেশের দরিদ্র কয়েকটা অঞ্চলের জন্য ২% কোটা রাখা যেতে পারে এবং প্রতি ৫ বছর পরপর তা পূর্ণমূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী উন্নয়নের সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়ন জড়িত। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ১০% কোটা বরাদ্দ ছিল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের জন্য। ১৯৮৫ সালে সকল নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তা এবং নামকরণ করা হয় ‘নারী কোটা’। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে মেয়েদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাতেও খুব বেশি তফাৎ নেই। নারী-পুরুষে সমতা অর্জনের বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৭তম। লিঙ্গবৈষম্য দূর করার প্রতিযোগিতায় ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশকে অনেক পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। ‘দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৭-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশ নারীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। ১৪টি সূচকের মধ্যে ৪ টিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১ নম্বরে।
তবে নারী-পুরুষ সমতা এসেছে একথা এখনি বলা যাবে না, তাই সীমিত পরিসরে নারী কোটা থাকা উচিত, তবে অবশ্যই তা ১০% নয়, সর্বোচ্চ ৫% হতে পারে। এ বিষয়ে ভেবে দেখার সময় এসেছে। বাংলাদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বলতে প্রথমেই আসে উপজাতিদের কথা। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৯ লক্ষ্য প্রায়—যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক শতাংশ মাত্র। ১% জনসংখ্যার জন্য ৫% কোটা রাখা কতটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখতে হবে।
তাছাড়া কোটা দ্বারা কেবল বৃহৎ কয়েকটি পাহাড়ী উপজাতি লাভবান হচ্ছে—সাঁওতাল, মুন্ডা, কোঁচ এর মতো সমতলের উপজাতি জনগোষ্ঠী এখনো অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাই উপজাতি কোটা কমানো এবং তা পাহাড়ী ও সমতলের মধ্যে সুষম বণ্টন করা উচিত। উপজাতি কোটা সর্বোচ্চ ২% যুক্তিসঙ্গত। মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১%-এর বেশি হবে না। অথচ সরকারি চাকরির ৩০% সংরক্ষিত রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য। অনেকেই বিষয়টাকে স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে দেখেন এবং এ বিষয়ে মৌনব্রত পালন করে থাকেন।
অনেকেই মনে করেন মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য পুরস্কার হিসেবে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা চালু করা হয়েছে। যদি এমনটা হয় তবে তা সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। যে বৈষম্য ও কোটারীর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল সেই কোটা আর স্বাধীন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেননি বঙ্গবন্ধু। কোটা চালুর কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হন। অনেকেই সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। তাই তাদেরকে অনগ্রসর ও ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার সরকারি চাকরির নিয়োগে ৩০% কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।
প্রশ্ন হলো—স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও কেন মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে বংশানুক্রমিক করা হচ্ছে? মুক্তিযোদ্ধা সন্তান প্রজন্ম কি অনগ্রসর? যদি তারা এখনো পিছিয়ে থাকেন তবে ৪৭ বছর থেকে চলে আসা কোটা ব্যবস্থার কার্যকারিতা কী? আমার পরিচিত অনেক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আছেন যারা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখেন! অথচ তাদের পরিচয় দেয়ার কথা বুক ফুলিয়ে। একবার ভেবে দেখেছেন ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহ?
কোটা দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোকে পরোক্ষভাবে অপমান করা হয়েছে, ছোট করা হয়েছে। নিজেদের সম্মান ও দেশটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে একাত্তরের সেসব বীরদের অাবারো এগিয়ে আসতে হবে। মানলাম এখনো অনেক মুক্তিযোদ্ধা দারিদ্র্যপীড়িত আছেন কিন্তু এই কোটা দ্বারা তাঁরা কি আদৌ লাভবান হচ্ছেন? বিভিন্ন পত্রিকা মারফত জানতে পারছি অনেক মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন!
দেশে শিক্ষিত বেকার জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার ছেলেমেয়েদের কান্না কেই শোনে না। বৈষম্য জিইয়ে রেখে, যুব সমাজকে কর্মহীন রেখে কখনোই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সময় এসেছে কোটা ব্যবস্থা পূণর্মূল্যায়নের। নাতি-পুতি বাদ দিয়ে ৫% মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা নির্ধারণ করে তা কেবলমাত্র দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা ও যেসব মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে কোনো সরকারি চাকরিজীবী নেই—এমন পরিবারের মধ্য সীমাবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি। নীতি নির্ধারকরা বলছেন মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটা চালু করা হয়েছে, তাহলে ব্যপারটা অসাংবিধানিক হয়ে যায়। তাছাড়া একথা দ্বারা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার বীরসেনানীদের অবদানকে ছোট করা হচ্ছে—কেননা জাতির সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের লাভের জন্য যুদ্ধ করেননি, যুদ্ধ করেছেন বৈষম্য থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে।
ধরে নিলাম যে রাষ্ট্র পুরস্কার হিসেবে কোটা চালু করেছে (যদিও তা সংবিধান সম্মত নয়) তাহলে ৩০ লক্ষ শহীদের পরিবার কেন কোটার আওতার বাইরে? বীরাঙ্গনা পরিবারগুলো কেন বঞ্চিত? যখন সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয় আর রাষ্ট্রই যদি হয় তার পৃষ্ঠপোষক তবে জাতীয় সংহতি চরমভাবে ব্যহত হয়। সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্র সমাজ আর এই শ্রেণি যখন বৈষম্যের শিকার হয়েছে তখনই হয়েছে বিপ্লব। ইতিহাস তাই বলে। আশা করি সরকার তরুণ সমাজের মনোভাব অনুভব করতে পারবে এবং তাদের যৌক্তিক দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।
৩৬ তম বিসিএসে (সাঃ শিক্ষা) ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত,
মেধাক্রম- ১ম (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)