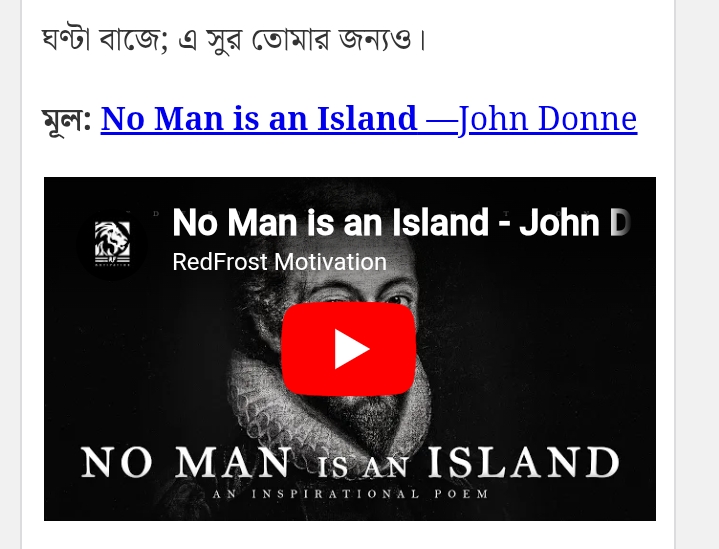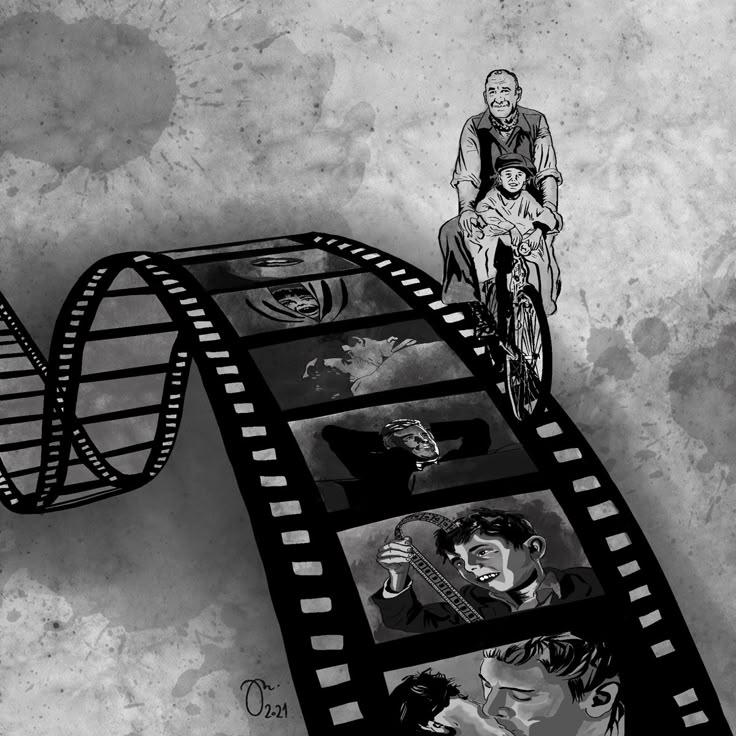আশ্রয়হীন, প্রশ্রয়হীন, অনিয়মিত জীবনযাপন মানুষকে যে শেষ পর্যন্ত অকাল মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছেন আমার পিতা। আমি সজ্ঞানে ‘বাবা’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘পিতা’ শব্দটি ব্যবহার করি। কারণ, ‘বাবা’ শব্দটি আমার মুখে আসে না। মনে আছে, তখন হয়ত আমি ক্লাস থ্রি অথবা ফোরে পড়ি, থ্রিই হবে। ওনাকে একবার পুলিশে ধরল, ঠাকুর বাড়ির কাউকে মারছিল বা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ, উনি বাধা দেয়ায় ওনাকে ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন আমাদের নাড়াকুটোর ঘরের সামনে এসে সেই ‘পুলিশ স্যারেরা’ ক্ষমাও চেয়েছিলেন। সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি মামাদের বাড়িতে বসে এক মাসিকে বলতেছিলাম, “গুণ্ডাকে পুলিশে ধরেছে ভালোই হয়েছে।” পরক্ষণেই আমি ভিরমি খেয়েছিলাম, এজন্যই কথাটা আমার এখনো মাথায় আটকে আছে।
আমার পিতা ছিলেন ‘ব্যাডলি বিউটিফুল’ অনেকের কাছে ‘বিউটিফুলি ব্যাড’। আমি যেহেতু বেশিরভাগ সময় মামাদের বাড়িতে কাটাতাম তাই মাসিদের বক্তব্যের সারাংশ আমার মধ্যে প্রতিথ হয়েছিল আমার অজান্তেই। আসলে ওনার প্রেমে পড়ে নাই, এমন নারী আমাদের এলাকায় ছিল না। আর পুরুষেরা বন্ধুত্ব করতো, পছন্দ করতো, প্রতিযোগিতা করতো, হিংসে করতো, শত্রুতাও করতো। ওনার সামনে কেউ শত্রুতা করতে সাহস পেত না, কিন্তু এ ধরণের মানুষের যে অনেক চাপা শত্রু থাকে সেটি বুঝেছি উনি মারা যাওয়ার পরে। [দাপুটে মানুষের প্রতি মানুষ আকরষিত হয়, আবার ঘোর কেটে গেলে এ ধরনের মানুষকে তারা সহ্য করতেও পারে না।] শত্রুতার মধ্যে আমরা দাদুর কারণেও পড়েছিলাম, যেহেতু উনি মারা যাবার পর আমরা শুধু মামা বাড়ির বাসিন্দা না, তাদের সবকিছুর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছিলাম। [শত্রুতা এক ধরনের চেইন। কোনো একজন সবল লোক যদি আপনার শত্রুতা করে তাহলে সমাজের দুর্বল লোকগুলোও এমনিই এমনিই আপনার শত্রু হয়ে যাবে। অশিক্ষিত সমাজে এটি ঘটে থাকে।]
আমরাও সেই চক্রে পড়েছিলাম। আমার পিতার অন্তর্নিহীতভাবে সবই ছিল, কিন্তু বৃত্ত ভাঙার সুযোগ ছিল না, ফলে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। উনি জীবনভর শুধু খেলাধুলা করেছেন, আর আড্ডা দিয়েছেন। অন্যরা আড্ডা দিতেন নির্দিষ্ট সময়ে, উনি আড্ডা দিতেন দল পরিবর্তন করে করে দিনরাত সারাদিন। বৃত্ত শেষ পর্যন্ত ভাঙলেন, তবে মহাশূন্য হয়ে।
পাড়া গায়ের একজন অসুস্থ মানুষকে এত বেশি মানুষে প্রতিদিন দেখতে আসতে পারে, সেটি বিস্ময়করই ছিল! উনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী, ফলে একদম মৃত্যু সায়াহ্নেও তাঁকে জীর্ণশীর্ণ মনে হয়নি কখনো। আমি কীভাবে যেন নিশ্চিত হয়ে গেলাম- উনি আর বাঁচবেন না। ফলে ঐ সময়ে আমার যা করার ছিল, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে তো আমার কিছুই করার ছিল না।
ফাইভে পড়ি, ছাত্র হিসেবে আমি সবসময়ই গড়পড়তা। কিন্তু ছোটোবেলায় অন্য সবার ধারণা ছিল- আমি মহা ভালো ছাত্র। ফলে আত্মীয়-স্বজনেরা, বিশেষ করে আমার মামা-মাসিরা আমার কাছ থেকে আশা করতেন অনেক। যেহেতু ওনাদের কাছে আমার পড়াশুনায় হাতেখড়ি, তাই তাঁরা আমাকে চিনতেনও ভালো। আমার যে মাসি ছোটবেলায় আমাকে পড়াতেন (তৃপ্তি মাসি), ‘ওনার মন্তব্য ছিল- আমার চেয়ে দ্রুত পিক করা নাকি কারো পক্ষে আর সম্ভব না।’ কিন্তু আমি যেটা বুঝতাম- একটু বড় হয়ে, এক অক্ষরও আমি মুখস্থ করতে পারি না, যেটা বুঝে উঠতে পারি না, সেটি শেষ পর্যন্ত পারিই না। ফলে বৃত্তি পরীক্ষায় যে গোল্লা পাব, সেটি আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম।
তখন পঞ্চম শ্রেণিতে ‘বৃত্তি পরীক্ষা’ হতো। বার্ষিক পরীক্ষার পর ‘ভালো শিক্ষার্থীদের’ দিয়ে আরেকটি পরীক্ষা দেওয়ানো হতো, এভাবে প্রতি উপজেলা থেকে কয়েকজনকে বাছাই করা হতো, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তাঁরা কিছু টাকা পেতো। সবচে বেশি হতো সুনাম [ছোটো বেলায় সুনাম বেশি হওয়া অবশ্য ক্ষতিকর বলে আমার মনে হয়]। শিক্ষার্থীর চেয়ে অনেক বেশি গর্ব করার সুযোগ পেতেন মাতা-পিতা।
উনি আমাকে একটা বৃত্তির বই কিনে দিলেন। সববিষয় মিলে তখন ‘বৃত্তির বই’ নামক একটা বই বের হতো। চার/পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা বই কিনে দেয়া ওনার জন্য খুব সহজ বিষয় ছিল না, কারণ, উল্লেখ করেছি- ওনার সবই ছিল কিন্তু টাকা ছিল না মোটেও। বড় মামা পড়াশুনার সুবিধার্তে আমাকে নিয়ে গেলেন বাগেরহাটে তাঁর বাসায়।
পড়াশুনা লবডঙ্কা, এমনিতেই বড় মামা খুব লেনিয়েন্ট, তার ওপর তিনি সবে বিয়ে করেছেন (ওনার বিয়ে হয়েছিল বেশ দেরিতে), পড়তে বসতে উনি কোনোদিনই বলেন না —সেটি ভালো লাগত, কিন্তু ওনাদের নতুন বিবাহীত জীবনে নিজেকে খুব ‘বাড়তি’ মনে হতো। সময় কেটে যেত ‘বাগেরহাট’ দেখে দেখে। সেই প্রথম জানলাম যে সিঙ্গাড়া ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক সুস্বাদু খাবার আছে, বেকারির দোকান থেকে দুই টাকা দিয়ে একটা নান রুটি (রুটির দুটো খণ্ডের মধ্যে সাদা সাদা ক্রিম দেয়া) কিনে পকেটে রেখে রোজ বিকেলে খেতাম। [পকেটে রেখে খাওয়াটা ছিল আমার সারা জীবনের অভ্যেস, মানুষের সামনে খেতে লজ্জা লাগত। পুরো স্কুল জীবন আমার কেটেছে পকেটে পিঁপড়া নিয়ে ঘুমিয়ে, আর পকেটে পিঁপড়া থাকলে সে পিঁপড়া কোথায় কোথায় যায় তা সহজেই অনুমেয়।] সম্ভবত আমি নিতাম বলে বড় মামা দুএক টাকা টেবিলের ওপর রাখতেন, কারণ, সবসময় আমি দুএকটা কয়েন সেখানে পেতাম। পড়াশুনা কিছুই হতো না। আমার তাতে কিছু যায় আসতও না।
একদিন বড় মামা হঠাৎ বললেন, বাড়িতে যেতে হবে। তখন পর্যন্ত জানি ওনাকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। একটা প্রশ্ন তখন আমার মনে দেখা দিয়েছিল, “ওনাকে নিয়ে মামারা কেউ গেলেন না কেন।” এখন বুঝি, যেহেতু বড় মামার সদ্য বিয়ে হয়েছে, তাই ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে পারেননি। অন্য মামারা তখনো খুব বড় নয়, এবং যেহেতু সবকিছু বড় মামাই সামলাতেন তাই তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কিছু করতে অভ্যস্তও ছিলেন না। ‘বাড়ি যেতে হবে’ কথাটার মধ্যে এমন কিছু ছিল—আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। উনি বইপত্র কেন গোছাতে বলছেন, তা-ও বুঝতে পারছিলাম না।
বাড়িতে আসলাম, এমন সময়ে আসলাম ঠিক যখন ওনাকে নৌকা থেকে নামাচ্ছে। তখন বর্ষকাল, আমাদের কাঁচা রাস্তা, তাই নৌকাই শয্যাশায়ী কাউকে বহন করার একমাত্র ব্যবস্থা। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। কিছু না বুঝেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম- ‘হি উইল বি নো মোর’, —চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে ফিরলে কেউ এভাবে তো ফিরবে না! আরেকটি বিষয় ছিল- আমাকে দেখেই উনি কেঁদে ফেলেছিলেন, সে কান্নাই সবকিছু বুঝিয়ে দিল।
খুব শক্ত মানুষ ছিলেন উনি, তাই খুব সহজে চোখে জল আসার কথা নয়। আমাদের নাড়াকুটোর ঘরের মধ্যে তাঁকে তোলা হলো —তখন শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। তবুও অন্তত একশোজন মানুষ লাগাতার ওনাকে যার যার মতো করে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। ওনার যে জায়গাটায় টিউমার হয়েছিল সেখানে পঁচন ধরেছে, শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে গেছে, ফলে যে কয়দিন বাঁচবে প্রয়োজন ছিল শুধু নার্সিং। ‘পঁচা গন্ধ’ সয়ে সেটি কে করবে? সেটি করল আমার এক মাসি, যে এখনো সুযোগ পেলে আমার মধ্যে, এমনকি আমার ছেলের মধ্যে ওনার ছায়া দেখতে পান। আমার মামাবাড়ীর সবাই যুক্ত হলেন তখন যখন উনি শতভাগ মৃত্যুপথযাত্রী। প্রতিদিন শতো শতো মানুষ ওনাকে দেখতে আসে, দূর দূরান্ত থেকে, যে যা পারে নিয়ে আসে। সেগুলো নিয়েও দেখি চাপা হিংসেহিংসি, কাড়াকাড়ি, লুকোনো চুরনো। এখন বুঝি লাগাতার দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা গ্রামের মানুষগুলোকে কতটা সংকীর্ণ করে তুলেছিল, এখনো তো সেরকমই আছে প্রায় সবাই। এই পঁচিশ বছরেও তো তেমন কিছু পরিবর্তন হতে দেখছি না, শুধু রাস্তাঘাট বদলেছে, বিদ্যুৎ ছিল না, বিদ্যুৎ এসেছে, অনেক ধরনের আয়োজন বেড়েছে, কিন্তু মনস্তত্ব আছে এখনও প্রায় সেই একই বৃত্তে।
ওনাকে দেখতে এসে কেউ একজন এক বোতল ফলের রস দিয়েছিল। লম্বা সাদা কাঁচের বোতলে বোতলজাত ফলের রস! দেখে তো অনেকের চোখ ছানাবড়া! বারান্দায় আপনজন মৃত্যুর জন্য দিন গুণছে, ভিতরে এসব চলে! আমি বিষাদগার করতে চাই না, কারো নাম বলতে চাই না। কিন্তু যে স্মৃতি মস্তিষ্কের মধ্যে সবসময় গেঁথে থাকে, মাঝে মাঝে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়, তা লেখা উচিৎ। এজন্য লিখছি। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় অধ্যায়টি বইতে ধরে রাখতে চাই। আমার ছেলেটা অন্তত জানবে, দায়িত্বশীল হবে। আমি আমার জীবনটাকে খুব দীর্ঘায়ু ভাবি না, না হলে এ লেখাটাতে আরো দশ বছর পরে হাত দেয়ার পরিকল্পনাই ছিল। কিন্তু ইদানিং মনে হয়- পিতা ৩৮ বছরে জীবন শেষ করেছেন, আমি সে পর্যন্ত না গেলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। খুব বেশি অতৃপ্তি যেন না থাকে সেজন্য মনের ভিতরে যে পরিকল্পনাগুলো খুব বেশি আঁকিবুকি করে সেগুলো শেষ করার চেষ্টা করি।
আমার দাদুর পরিবার ছিল গ্রামের অভিজাত পরিবার, দিদিমা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, তবে তাঁরাও ছিলেন বৃত্তবন্দী মানুষ। অভিজাত হওয়া ভালো, কিন্তু সেটির প্রকাশ এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সামান্য উগ্রতা প্রকাশ পেলেও তা ভযঙ্করভাবে বুমেরাং হয়। ওনাদের ক্ষেত্রে সেটি হয়েছিল, বোঝার আগেই ব্যপ্ত হতে চেয়েছিলেন। মানবিকতাবোধে অন্য অনেক মানুষের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিক সচেতনতার অভাব ছিল তাঁদের, অল্প জেনে বা কিছু না জেনেই মামাদের পরিবারটা ভেবে ফেলা অভ্যেস করে ফেলল যে তাঁরা সব জেনে গেছে, এখনই সবখানে সামনের চেয়ারে বসে পড়া যায়। সবখানে সামনের চেয়ারে বসতে গিয়েই তাঁরা ডুবেছে। তাই বলে ফলের রস নিয়ে কাড়াকাড়ি বা মৃত্যুপথযাত্রীকে কে কী খাবার দিয়ে গেল সে হিসেবে রাখার মতো সংকীর্ণতা তাঁদের মধ্যে ছিল না।
বিশাল সম্পদ নিয়েও দাদু কোনোদিন ধনী হতে পারেননি বেহিসেবী এবং অপরিকল্পিত হওয়ার কারণে। তিনি ছিলেন সৎ, স্পষ্ট, এবং ভুল একজন মানুষ। ফলে তাঁর কাছ থেকে কোনো অপরাধ আশা করা যায় না। তাঁরা ছেলে-মেয়েরাও প্রায় সবকজন তাঁর মতোই। দিদিমা সর্বংসহা, কর্মঠ, সমাজে অন্য নারীদের মতোই বঞ্চিত। তখন তো অবশ্যই, এখনও নারীদের ‘সততার’ প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন শুধু অবোধ্য সতীত্বের, সেরকম প্রশ্নটুকুও ওনাকে নিয়ে ওঠেনি কোনোদিন—এক কথায় শতভাগ ক্লিন ইমেজের মানুষ উনি। শুধু ত্যাগই করেছেন, এবং অনেক ভুলও করেছেন, ভুলগুলো অন্য নারীদের মতোই পারিবারীক, কিন্তু সে ভুলের পরিণাম পারিবারীক গণ্ডির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, থাকেনি।
আমার পিতার তখন একমাত্র খাদ্য দিদিমার হাতের ঝাল না দেয়া খিচুড়ি, আর একমাত্র সন্তুষ্টি মানুষের ভালোবাসা, ছোটো মাসির শুশ্রূষা। এতো মানুষ! এতো মানুষ প্রতিদিন আসত, ভাবা যায় না!! সাধারণ একজন মানুষের এরকম বর্ণাড্য মৃত্যু আমি আর দেখিনি। মৃত্যুর পরে এরকম নিরবতা এবং শত্রুতাও আমি এর চেয়ে বেশি আর অন্দাজ করতে পারি না।
ওনাকে বাঁচানোর জন্য একেকজন একেক দাওয়াই দিচ্ছে, কেউ কালির ‘বার’ পড়ছে, কেউ মঁনশার বার পড়ছে, কেউ নিজেই ‘ঈশ্বর’ হয়ে উঠছে। সুস্থ মানুষ আমাদের উঠোনে ভিরমি খেয়ে পড়ে এটা ওটা বলত তখন। এরকমই একজন বললেন, ওনাকে যদি একশো রকমের গাছের পাতা রস করে খাওয়ানো যায় তাহলে বেঁচে যাবেন। কে সংগ্রহ করবে একশো রকমের গাছের পাতা? আমি দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু একদিনও তাল রেখে আমি ঠিক একশো রকমের পাতা সংগ্রহ করতে পারিনি। একশো রকমের গাছ অবশ্যই গ্রামে আছে, কিন্তু কোনটি নিলাম আর কোনটি নিলাম না সে হিসেব ঠিক রেখে কাজটি করা সহজ ছিল না। তাছাড়া অনেক পাতা একই রকমের, ফলে একবার মিশে গেলে আলাদা করে গোণাও সম্ভব ছিল না। পুরো একটা পাতা নিতাম না, কারণ, আমার মনে হতো এর মধ্যে কোনো পাতা যদি বিষাক্ত হয় তাহলে তো সেটির জন্য খাওয়ার সাথে সাথে উনি মারা যাবেন। পাতা নিতাম একটু একটু, এ কারণে গুণতে সমস্যা আরো বেশি হতো। ৫২ পর্যন্ত আসলাম, নাকি ৫১? পরে একশো হয়ে গেছে জেনেও আরো কয়েকটি তোলার চেষ্টা করতাম যাতে কম না হয়।
শেষ পর্যন্ত উঠোনে বসলো ‘ঈষ্ট নামের আসর’ —এটি ছিল আরেকজনের পরামর্শ। পুরো উঠোন জুড়ে টিনের ছাপড়া করে নেয়া হলো। প্রতিদিন অনেক মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে কিছু না কিছু টাকা দিয়ে যেত। এভাবে সম্ভবত ৫০,০০০/- উঠেছিল শেষ কয়েকদিনে। উনি বলতেন ওনাকে ঢাকায় নিয়ে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে, কারণ, তাক কলকাতায় নেয়া হয়েছিল শুধু, চিকিৎসা করানো হয়েছিল না, যারা নিয়ে গেছিল তাঁদের অর্থনৈতিকভাবেও সে ক্ষমতা ছিল না, আবার জানা শোনাও ছিল না, ফলে একটা ‘ভ্রমণ’ হয়েছিল মাত্র।
ওনার ইচ্ছে পূরণ করতে শেষে গিয়ে বড় মামা, দিদিমা, অসীম কাকা, বড় পিসি রওনা হলেন ঢাকার উদ্দেশ্য। হুলোরহাট (পিরোজপুরের হুলোরহাট লঞ্চ ঘাট) থেকে লঞ্চে ঢাকা যাবেন। হুলোরহাট পর্যন্ত আমি গিয়েছিলাম। নৌকা থেকে ওনাকে তোলা হলো, অনেক ঢেউ নদীতে, এই বুঝি ডুবে গেল নৌকা, খুব ভয় পেয়েছিলাম।
আমরা সবাই মামা বাড়িতে চলে গেলাম — মা এবং আমরা চার ভাইবোন। টানা এক মাসের ভীষণ ক্লান্তি, হতাশা, বিপন্নতা, গ্লানিবোধ; একটু হাঁপছাড়ার সুযোগ হলো। দাদু বাধাল হাট থেকে পেয়ারা নিয়ে এসেছিলেন, পাকা পেয়ারার একটা ঘ্রাণ আছে, ঐ দিনের ঐ ঘ্রাণটা এখনো আমার নাকে লেগে আছে। ঐ দিন আমরা বোধহয় একটু রাত করেই ঘুমিয়েছিলাম। বারোটার দিকে মাসিকে বললাম, আমার খুব ভয় করছে, কাঠের বেড়ার একটা খুঁটি দেখিয়ে বললাম, লাল লাল কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে, মূলত আমি এক ধরনের ট্রমার মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত এরকম ট্রমার মধ্যে ছিলাম।
তখন মোবাইল ছিল না, তাৎক্ষণিক যোগাযোগের কোনো সুযোগও ছিল। আমরা হিসেব করছিলাম, লঞ্চটা কখন ঢাকায় পেঁৗছবে, কীভাবে চিকিৎসা হবে, কোথায় থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি। লঞ্চে চড়ে ঢাকায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে যাদের তাঁদের কাছে জানার চেষ্টা করছিলাম লঞ্চটা কখন ঢাকায় পৌঁছবে। জানলাম, লঞ্চ সকাল সাতটার মধ্যে ঢাকায় পৌঁছে যায়। “তাহলে চিকিৎসা শুরু হতে নিশ্চয়ই নয়টা বাজবে” এ ধরনের নানান হিসেব। দিনটা কাটল যুগসমান দীর্ঘ হয়ে।
রাতটা আর কাটল না। ভোর না হতেই বড় মামাকে দেখে চমকে উঠলাম! বড় মামা না বাবাকে নিয়ে ঢাকায় গেলেন!! তেমন কিছু না বলে বড় মামা আমাদের সবাইকে নিয়ে দ্রুত পাশের গ্রামে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলেন। কাছাকছি পৌঁছে শুনতে পাচ্ছি বাড়িতে তখন অপর্যাপ্ত ক্রন্দন রোল, আগন্তুকরা পর্যাপ্ত দূরত্বে দাঁড়িয়ে।
ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেছে মৃতদেহটা। মারা গেছেন ১৫ শ্রাবণ শেষ রাতে (৪টায়), ঢাকায় পৌঁছে একটা ট্রাকে করে মৃতদেহ নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে পেরেছেন পরের দিন শেষ রাতে। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে মৃতদেহটা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। আসলে ওনার দেহের সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছিল, কাঠামোটা শক্তপোক্ত ছিল বলে উপরে একটা আবরণ ছিল মৃত্যর আগ পর্যন্তও।
এবার মানুষের আসল চরিত্র দেখার পালা। তারপরও আমি মানুষকে দোষ দিতে চাই না, আমি মানুষকে সবসময় দেখি পরিস্থিতি এবং পরিবেশের শিকার হিসেবে। কিন্তু সে ছিল এক অব্যক্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি। আসলে উনি মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছিল। মানুষ যে শত্রুতার খেলা খেলতে পছন্দ করে, এবং খেয়ে না খেয়ে থাকা সাধারণ মানুষ তা আরো বেশি করে, সেটি আমি ছোটো বেলাতেই বুঝেছিলাম পরিষ্কারভাবে।
সনাতন রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকার করা অনেক নিয়মকানুনের বিষয়। কেউ এগোচ্ছে না, যে টাকাগুলো জমা আছে সেটিও বের করছে না। টাকাটা বড় মামার কাছে ছিল না। লেখাটা আরো অগ্রসর হলে সেসব কথা আসবে।
আমি বড় মামাকে পরে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, “বৃষ্টির মধ্যে আপনারা পাঁচজনে (চারজনে) মৃতদেহটা নিয়ে ট্রাকে আসলেন কীভাবে?” উনি বললেন, “আমি আর মা তোর বাবার সাথে ট্রাকে ছিলাম।” তাহালে সম্ভবত কাকা আর পিসি বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে সিটে। এর আগেই কাকা এবং পিসির সাথে বড় মামার একটা বচসা হয়েছিল লঞ্চের কেবিনে বসে। ওনারা চেয়েছিলেন মৃতদেহটা নদীতে ফেলে দিতে!
আমাদের আপন কাকা নেই, পিতার এক বড় ভাই ছিলেন ইন্ডিয়াতে, তাঁর নিজেরই কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। এই কাকারা ওনার কাকাত ভাই, এনারা খুব কষ্টে বড় হয়েছেন, ভীষণ কষ্টে — দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটতে দেয় না, তাইই হয়ত হয়েছিল ওনাদের ক্ষেত্রে তখন। এই কাকাকে দেখেছি ছোটবেলা থেকেই খুব কষ্ট করতে, হেন কোনো কাজ নেই তিনি করেননি। খুব ছোটবেলায় ওনার কাছ থেকে তালের রস খেতাম। দুপুর বেলায় তালের রস খেতে অনেক মজা।
[আমি কাউকে দোষ দিই না, শুধু বুঝতে চাই যদি ঐ ‘অনুশোচনাটুকু’ তৈরি হয়ে থাকে, যদি মানুষ শুধরিয়ে থাকে। না হলে মানতে পারি না — সবকিছু ছারখার করে দেয়ার মতো শক্তি এবং জীবনকে নিমিষে তুচ্ছ করে দেয়ার মতো অভিজ্ঞান তো ভিতরে তৈরি হয়ে আছে।]
কিন্তু আমার বড় পিসির কী হয়েছিল? নাকি উনি উত্তর আধুনিক যুগের বাস্তববাদীদের মতো ‘অতি উদার’ মানুষ ছিলেন, হয়েছিলেন? মৃতদেহ নিয়ে পড়ে থাকাতে, বাড়ি ফেরাতে বিশ্বাসী ছিলেন না উনি? একটা সময়ের পরে আমার ওনার (এই পিসির) জন্য খুব মায়া হয়, নিশ্চয়ই ওনার মধ্যে এসব নিয়ে অনুশোচনা আছে। ‘অনুশোচনা’ খুব মহৎ জিনিস, এটা সবকিছু খাটি করে দেয়। আবার এও বুঝি- অশিক্ষা মানুষকে পুরোপুরি অন্ধ করে দিতে পারে, নিজের চোখ দিয়ে মানুষ তখন কিছুই দেখতে পায় না।
লাশ সৎকার করতে কেউ এগিয়ে আসল না। সেদিনও বোধহয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, উঠোনে ওনার সাদা ফোলা পায়ের তলা দিয়ে মায়ের কপালের সিঁদুর মুছে দেয়া হলো। আমি বড় ছেলে, নিয়ম সব আমারই করতে হবে। বড় ছেলে হলেও আমার বয়স তখন ১০ বৎছর ৩ মাস! দাদু মৃতদেহ সৎকারে এগিয়ে আসলেন, উনি আজীবনই এগিয়ে আসা মানুষ ছিলেন, এদিক থেকে জামাই শশুরে মিল ছিল। বাড়ির মানুষ বাড়ির মধ্যে সৎকার করতে দিলেন না ‘দুর্গন্ধ’ ছুটবে বলে! নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ি থেকে দূরে খাল পাড়ে। বৃষ্টির দিন, কাঠ নেই, কিছু শুকনো কাঠ তো লাগবে। আশেপাশের যাদের বাড়িতে কাঠ আছে কেউ দিতে রাজি নয়। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ভীষণ এক উল্টো চিত্র দেখছি- শয্যাশায়ী জীবিত মানুষের এত খাতির, আর এখন কেউ এক মুঠো শুকনো কাঠ দিতেও রাজি নয়! বুঝলাম, এখন বুঝি, সাধারণ মানুষ সচেতনভাবে তেমন কিছু করে না, তাঁরা করে ভয়ে, মোহে, ভুলে, আকর্ষণে, হুযুগে। ক্রমাগতভাব বঞ্চনার অনুভূতি লালন করতে করতে তাঁরা কোনো দিশা খুঁজে পায় না।
সবকিছু উল্টে গিয়ে শুরু হলো আমাদের অবহেলা করার হুযুগ। সে হুযুগ এখনো চলছে দেখে বিস্মিত হই, অনেকের অনুশোচনা তৈরি হয়নি দেখে বিস্মিত হই। ইতিবাচক বিস্ময় থেকে জন্ম নিতে পারে সুন্দর ভালোবাসা, নেতিবাচক বিস্ময় থেকে জন্ম নেয় ক্ষোভ, লাগাতার ক্ষোভ থেকে তৈরি হয় দাবানাল। সে দাবানলে বিষাক্ত কীটে ধরা পুরাতন সবকিছু পুড়ে যায়, তৈরি হয় নতুন মানুষ, নতুন আবাস, নতুন পৃথিবী।
স্মৃতি থেকে তুলে আনো দিন,
বুকের মধ্যে দাউ দাউ
করে জ্বলেছিল আগুন,
যে আগুনে পুড়ে তুমি খাটি হয়েছিলে।
নিভতে দিও না, দাবানল হয়ে
ছড়িয়ে পড়ুক চারিদিক—
যতদিন সভ্য না হয় এ প্রান্তর।
-চলবে।