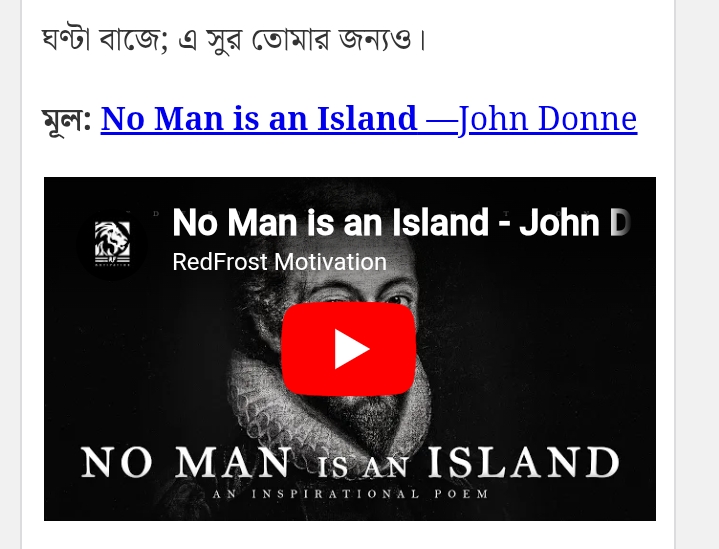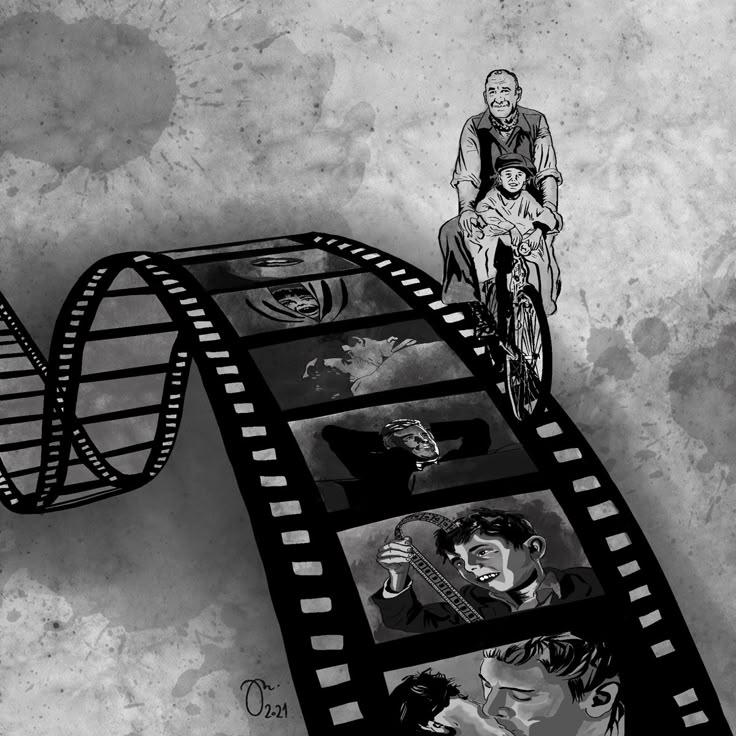মুক্তিযুদ্ধ তখন কেবল সবে শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মানে শুরু করতে বাধ্য হয়েছে বাংলার মানুষ। এটা মুক্তির যুদ্ধ, আবার বাঁচার যুদ্ধও। এতদিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বিবাদে মেরে ফেলেছে পাকিস্তানী বাহিনী রাজাকারদের সাথে নিয়ে। রাজাকার কারা হয়েছে–অনেকেই হয়েছে, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে হয়েছে, ঘৃণা এবং প্রতিহিংসাই এর মধ্যে সবচে’ বড় কারণ।
তবে রইসুল্লা হোক্কার ক্ষেত্রে কারণটা ভিন্ন, আবার সে ঠিক রাজাকার নয়, বরং তাকে ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধাই বলতে হবে, মুক্তিবাহিনী তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই জানে, শুধু তার খুব কাছের দু’একজন জানে তার আসল পরিচয়। তবে তারাও মারা যায় দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই।
তারিখটা সম্ভবত ২এপ্রিল ছিল, ঢাকায় তখন পাকিস্তানী বাহিনী এবং বিহারী-রাজাকারদের দাপট, মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে গণহত্যা চালিয়েছে ওরা জগন্নাথ হল, শাঁখারিবাজার, তাঁতী বাজার, বাবু বাজার, সদরঘাট, মালাকারটোলাসহ ঢাকা শহরের আরো অনেক জায়গায়, প্রথমদিকে প্রধানত হিন্দুদের টার্গেট করা হয়েছিল, এরপর তারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙ্গালী নিধনে মেতেছে।
বেশিরভাগ হিন্দু পরিবার এই কয়দিনে ঢাকা ছেড়ে গিয়েছে, অনেকে বুড়িগঙ্গার ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যাদের সুযোগ আছে তারা ভারতে চলে গিয়েছে। বুড়িগঙ্গার ওপারে গিয়েও রেহাই হয়নি, হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তারা, জিঞ্জিরা গণহত্যায় মারা গিয়েছে অনেকে।
বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরা এলাকা ছিল তখন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। জিঞ্জিরা, কালিন্দি ও শুভাড্যা -এই তিন ইউনিয়ন মিলে গণহত্যাটি সংগঠিত হয়েছিল। ভোররাত থেকে সৈন্যরা মোতায়েন হয়ে আট থেকে নয় ঘণ্টাব্যাপী চালিয়েছিল এ গণহত্যা। নারী ও শিশুসহ কয়েক হাজার লোক মারা যায় জিঞ্জিরা গণহত্যায়।
জিঞ্জিরা গণহত্যায় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে অংশ নিয়েছিল রইসুল্লা হোক্কার মত অনেকে। ঘৃণা-প্রতিহিংসা ভেতরে বর্বরতা এতদিন পুষে রেখেছিল হোক্কা, কিন্তু তার প্রকাশ যে এতটা প্রকাশ্য, এতটা কুৎসিত হতে পারে তা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না আজ! যদিও তার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান বাহিনীকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা, কিন্তু নৃশংসতা, বাধাহীন বিভৎসতা দেখে তার বর্বর সত্তা জেগে ওঠে।
রইসুল্লা গোলাগুলির মধ্যেই সুযোগ খুঁজতে থাকে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হৈ হট্টগোল, আর্তনাদ তাকেও বিচলিত করে, একবার এক পাকিস্তানী সৈন্য তাকে “ছালা শুয়ারকা বাঙ্গালী আদমী” বলে কষে পাছায় লাথি মারে, রইসুল্লা ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে অপেক্ষা করছে হত্যাকাণ্ড কখন শেষ হয়। দুপুর গড়িয়ে থামে জিঞ্জিরা হত্যাযজ্ঞ।
রইসুল্লা মৃতদেহ খুঁজে খুঁজে টাকাপয়শা সোনাদানা যা পায় নিয়ে নেয়, এর মধ্যে শুভাড্যায় একটি একতলা বাড়ি থেকে গোঙ্গানীর শব্দ ভেসে আসে–নারীকণ্ঠের ক্লান্ত সুরের আর্তনাদ। রইসুল্লা ঘরে প্রবেশ করে, দু’তিনটি মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে, ষোলো সতের বছরের একটি মেয়ের পেটের একটু উপরে গুলি লেগেছে, রক্ত বন্যা বয়ে যাচ্ছে। রইসুল্লা মেয়েটিকে ঐ অবস্থায় অনাবৃত করে নির্যাতন করে, কয়েক মুহূর্ত পরেই মেয়েটি মারা যায়। টাকা পয়শা গয়নাগাটি যথেষ্ট পরিমাণ কুড়িয়ে সে চলে আসে এ পারে।
বাবু বাজারের দিকে বুড়িগঙ্গা ঘেষে একটি একতালা ছোট্ট বাড়ি ছিল রইসুল্লাদের, সোনাদানাগুলো সে বাড়ির পাশে ঝোপের মধ্যে মাটিতে পুতে রাখে। প্রায় ষাট সত্তর হাজার নগদ টাকা সে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। টাকাগুলো সে খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে–সে উভয় পক্ষের সাথে থাকতে চায়। বিহারীদের সাথে রইসুল্লা ঐদিন রাতেই যোগাযোগ করে, তাদের বেশি কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করে।
মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে সে খোঁজখবর রাখত, এলাকার মুক্তিপন্থীদেরও সে সাহায্য করতে চায়। ন্যাপ নেতা সামাদ রহমানকে সে বলে, আমার তো তেমন কিছু নেই, বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র বেঁচে দিয়ে এই দশ হাজার টাকা আপনাদের দিলাম–দেশের জন্য কিছু তো করতে হবে। ভাববেন না, ডাক দিলেই পাবেন।
একটু গভীর রাতে বিহারী নেতা বাচপানকে সে বাড়িতে ডাকে। গেণ্ডারিয়ায় একটি বাড়ির ওপর তার অনেকদিন ধরে চোখ, বাচপানকে সে বলে, তুমি থাকবা কিনা কও, ট্যায়া পয়শা সব তুমি নিবা, আমার কাম এইহানে ভিন্ন। বাচপান রাজি হয়ে যায়। আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে পরিবারটি এখনো পালায়নি। গেন্ডারিয়া তখনো অতটা ঘনবসতি নয়, সেখানে পাক বাহিনীর সরাসরি আক্রমণ হয়নি।
বাড়িটিতে তপন সাহা, তার স্ত্রী সাবিত্রী এবং এক সন্তান ছিল। ছেলেটির বয়স আট বছর। তপন সাহার নারায়নগঞ্জে কাপড়ের ব্যবসা ছিল। ঐদিন সে একটু দেরিতে ফিরেছে, রাত বারোটার দিকে শঙ্কা নিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।
রইসুল্লা বাচপান এবং আরো তিনজন গুণ্ডা নিয়ে বাড়িটিতে হানা দেয়। পরিকল্পনামাফিক একজন বাইরে থাকে, সে বাড়িটির প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেবে। অন্যরা অস্ত্রহাতে বাড়িতে প্রবেশ করবে। সন্তান নিয়ে এক ঘরেই ঘুমিয়ে ছিল তপন সাহা এবং তার স্ত্রী। বাইরে থেকে জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে থাকলে ভেতরে ওরা তটস্থ হয়ে থাকে।
দরজা না খুললে, বাচপান এবং রইসুল্লা কাঠের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে, পিছনে আরো দুইজন। পরিকল্পনামাফিক একজন বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেয়। তপন সাহার স্ত্রী সাবিত্রী এসে রইসুল্লার পায়ে পড়ে, রইসুল্লা অনেকদিন থেকে তাকে বিরক্ত করছে, তাই দেখেই সে তাকে চিনতে পেরেছে।
রইসুল্লা বলে, বইন আমার–শোন, কাউকে মারব না, আমার দিলে বহুত দরদ আছে, কাউরে মারব না–একথা বলে হাতের ইশারায় তপন এবং তার সন্তানটিকে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে বলে। এই ঘরে শুধু রইসুল্লা থাকে। সাবিত্রী বেরিয়ে যেতে চাইলে হ্যাচকা টান দিয়ে তাকে খাটের উপর ফেলে দেয়।
“শোন, এই জিভ থেকে মণকে মণ লালা ঝরেছে এদ্দিন, বুড়িগঙ্গায় মিলায়ে গ্যাছে, তুই কি তা জানস খানকি? জানস না, জানবি না, তুই তো দেবী, দেবী দুগ্গা এক্কারে, আমি দেবীর কাঙ্গাল, আমি রইসুল্লা দস্যু দেবী খুঁজি, পাইছি তরে, খামু আইজকে, পরাণডা ভরে খামু, চার হাত-পা দিয়ে খামু।”
সাবিত্রীর নাভীর পাশে পোচ দিয়ে রক্তাক্ত করে উল্লাস করতে থাকে সে, যেন কল্পিত নরক হতে সত্যিই কোনো দানব নজীরবিহীন বর্বরতায় মেতেছে। হঠাৎ পাশের রুম থেকে গুলির শব্দ অাসে–এক, দুই, তিন, চার, পিতা-পুত্রের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কিছুক্ষণ। সাবিত্রী জ্ঞান হারায়। অজ্ঞান সাবিত্রীকে নির্যাতন করে হত্যা করে রইসুল্লা হোক্কা। লাসগুলো ওরা নির্বিঘ্নে সেদিন বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসে। বাড়ির সবকিছু লুটে নেয় বাচপান এবং অন্য তিনজনে। হোক্কা শুধু বাড়িটির তালাচাবি নিজের কাছে রাখে।
এরপর হোক্কা এক বুদ্ধি আটে, সে ঐ বাড়িটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প করে দেয়। যুদ্ধকালীন মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়, খাদ্য খাবারও পাঠায়, বলে, বাবারা চাইলেও স্ত্রী-পুত্র ফালায়ে যুদ্ধে যাওয়ার কলিজা আমার হয় না, তোমরা বীর, তোমাদের তাই কিছু খাওন দিয়ে যাই মাঝে মাঝে।
এদিকে রাজাকারদের সাথে তার ওঠাবসা, তাদেরকে কিছু একটা সন্ধান দিতে হবে, নইলে মান থাকে না। অগাস্টের শেষের দিকে লম্বু রাজাকাররে সে জানায়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ ক্যাম্পের কথা। ঐদিন রাতেই লম্বু রাজাকার পাকিস্তানী বাহিনী নিয়ে হানা দেয় ক্যাম্পে, দু’জন মুক্তি বাইরে ছিল বলে বেঁচে যায়, বাকী সবাই মারা যায়।
বেঁচে যাওয়া দু’জনকে অনেক স্বান্তনা দেয় রইসুল্লা, কিছু টাকা পয়শাও দেয়। ঐ দুই মুক্তিকে জানায়ে দেয় তিনজন গুণ্ডা রাজাকারের কথা, যাদের সাথে নিয়ে সে তপন সাহার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। রাতে কোথায় তাদের পাওয়া যাবে তাও তাদের জানিয়ে দেয়। ঐদিন রাতেই তিন গুণ্ডা মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত হয়।
এরপর রইসুল্লা হোক্কা কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে সে আবার সামনে আসে। ঐ বেঁচে যাওয়া দু’জন মুক্তিযোদ্ধাকে আরো কিছু সাহায্য করে। বাচপান সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে সে ইতোমধ্যে দেশ ছেড়ে গেছে। রইসুল্লা বাক্সপেটরা নিয়ে গেণ্ডারিয়ার ঐ বাড়িটিতে উঠে যায়। মুক্তিবাহিনীর অনেকের খোঁজ খবর নেয়, বাড়িতে অনেককে আশ্রয়ও দেয় কিছুদিন।
সে এখন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা, সে যে মুক্তিযোদ্ধা সে সাক্ষীরা–ঐ দু’জন ডাকসাইটে মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে ছিল, তাই গেজেটে তার নাম উঠে যায়। বাড়িটিও খুব সহজেই নিজের নামে করে নিতে পারে, ঐ সময় সবাইতো আর বাড়ি লিখে দিয়ে যেতে পারেনি, কে কার খোঁজ নেয়! আর রইসুল্লা যেহেতু নামকরা মুক্তিযোদ্ধা, তাই তাকে সন্দেহ করার প্রশ্ন নেই।
বাড়িটি এখন বহুতল হয়েছে, রইসুল্লা হোক্কার নামটাও একটু বদলেছে–গেণ্ডারিয়া এলাকায় তাকে এখন সবাই মুক্তিযোদ্ধা রইসুল্লা গাজী নামে চেনে। স্বাধীন বাংলাদেশে সে উন্নতি করতে পেরেছে খুব দ্রুত, টাকা গয়নাগাটি জমি জাতি মিলিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়া মাত্রই তো সে একজন ধনাড্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। ধন-দৌলত, খ্যাতি-প্রীতি সবই হয়েছে এক ঝটকায়।
সন্তানরা বড় হয়েছে। দু’একজন তার ব্যবসা দেখে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভালো চাকরি পেয়েছে। তার চৌদ্দ সন্তানই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দু’জন সরকারের বড় আমলা হয়েছে।
বছর দুই হল গাজী মারা গিয়েছে। এলাকায় নামডাক নিয়ে বেঁচেছিল সে, প্রচুর দান-ধ্যান করেছে, সম্মানের সাথেই সে মারা গিয়েছে। পাথর খোদাই করে কবরের সামনে লেখা হয়েছে–“বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রইসুল্লা গাজী, জন্ম: ১৩ই শ্রাবণ ১৩৩৭, মৃত্যু: ৮ই কার্তিক ১৪২১।”
গল্পটি লন্ডনপ্রবাসী লেখক শেকস্ রাসেলের গল্পগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত