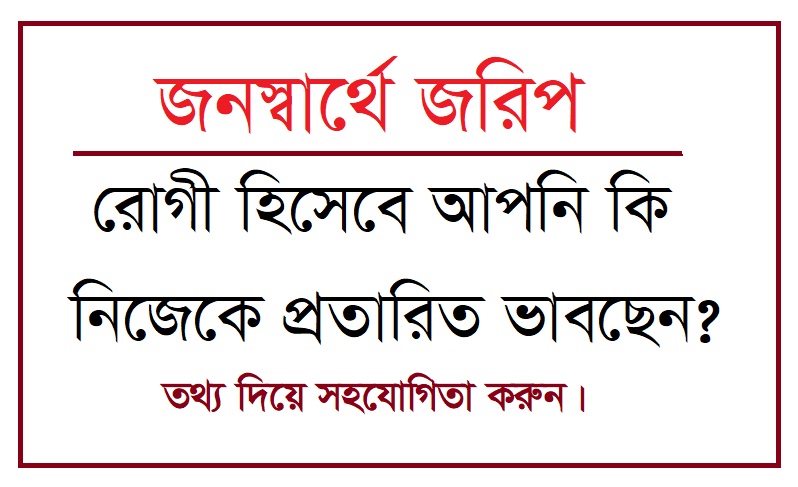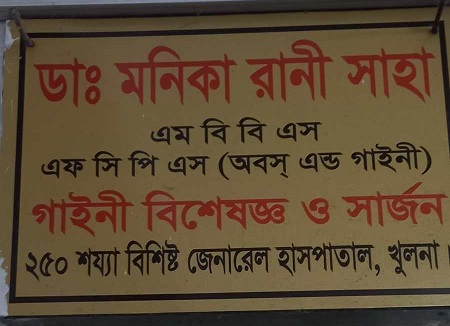আমি ফরিদুপুর যাই ১৬ তারিখ (১৬ মার্চ ২০২১)। ঈশপকে একটা স্কুলে ভর্তি করে ঈশপ এবং ঈশপের মা’কে আবাসিক থাকার ব্যবস্থা করব, আমি একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব এবং একটা স্মরণিকা বের করব। এরপর বাগেরহাট যাব। উঠেছি সাজ্জাদ ভাই এবং বীনা ভাবীদের বাসায়। স্মরণিকার কাজটা করছি, ২০ তারিখ পর্যন্ত আমি নির্বিঘ্নে কাজ করেছি। সম্ভবত বিশ তারিখ বিকাল থেকে আমি অসুস্থ বোধ করি। প্রচণ্ড সর্দি, হালকা কাশি এবং গা একটু গরম গরম। ২৬ তারিখ অনুষ্ঠান, স্মরণিকাটা তার আগেই বের করতে হবে। অসুস্থতাকে খুব বেশি পাত্তা না দিয়ে আমি কাজ করতে থাকি। কভিড-১৯-এর কথা আমার মাথায় আসে ২২ তারিখ রাতে। এদিন থেকেই মূলত বেশি খারাপ লাগা শুরু হলো। ২৩ তারিখে সকালে ফরিদপুর সদর হাসপাতালে গিয়ে টেস্ট করতে দিয়ে আসলাম।
বিকালে ল্যাবএইড থেকে বুকের একটা এক্সরে এবং ব্লাড টেস্ট (সিবিসি) করায়ে এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার ব্লাড রেজাল্ট এবং এক্সরে দেখে বললেন করোনার টেস্ট করতে, একইসাথে প্রেসক্রিপশনও করলেন। আমি তো করোনার টেস্ট আগেই করতে দিয়েছি। ২৩ তারিখও আমি প্রেসে বসে স্মরণিকার কাজ করলাম। ২৪ তারিখ মোবাইলে মেসেজ আসলো আমি পজেটিভ। ২৪ তারিখ ঈশপের মা ছাড়া আমি আর কাউকে জানালাম না, তাহলে স্মরণিকা এবং অনুষ্ঠান সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। মাথায় মাফলার পেঁচিয়ে মুখে ডাবল মাস্ক লাগিয়ে আমি স্মরণিকার কাজ করে গেলাম।
২৫ তারিখ স্মরণিকাটা প্রেসে দিয়ে আর পারলাম না– এসে বিছানায় পড়ে গেলাম। ঐদিনই সবাইকে জানালাম। ফেসবুকে স্টাটাস দিলাম। লক্ষ্মী ভাবীরা কেউ ভয় পেলেন না, আমার সেবা শুশ্রুষায় মনোযোগী হলেন। আন্টি (লক্ষ্মী ভাবীর মা) এবং ভাবী দুজনই খাবার দাবার নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। ভাবীর মেয়েটা (মৌটুসি) তো ঈশপকে অনেক সময় দিয়েছে। কিন্তু আমি খেতে পারছিলাম না। ২৬ তারিখ ফরিদপুরের শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিশাল অনুষ্ঠান, তাই অসুস্থতা যথাসম্ভব চেপে রাখলাম। ২৬ তারিখ রাতে অবস্থা খুব খারাপ হলো। ভয়ানক ছটফটানি গেলো সারারাত। ইতোমধ্যে সজলের কাছ থেকে শুনে স্কাবো খেয়েছি, ডক্সিসাইক্লিন খাচ্ছি। সজলও কভিড-১৯ পজেটিভ। সজল ফিট, আমি নিশ্চিত জানি সজলের কিছু হবে না। সজলের সাথে মোবাইলে কথাবার্তা চলছে।
২৭ তারিখ সকালে মামাবাড়ী থেকে বলাই মামা আসলো। সুবর্ণা এবং মামার সাথে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। একটা বসার চেয়ারও সেখানে নেই। বুঝলাম না এ ধরনের রোগীরা কীভাবে ভর্তির সময় দাঁড়ায়ে থাকবে! আগে বেডে পাঠিয়ে দিয়েও তো ভর্তি করা যায়। অথবা সহজ কোনো একটা উপায় বের করা যায়। এগুলো এমন কিছু না, জাস্ট রোবটের মতো চাকরি না করে একটু মানবিক হওয়ার বিষয়। এজন্য কোনো নিয়ম লাগে না, আবার নিয়মের ব্যত্যয়ও হয় না। আধা ঘণ্টা আমি গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। মাথা ঘুরে ছিটকে পড়ে যাই। অবশেষে বেডে গিয়ে শুলাম। সাথে সুবর্ণা এবং ঈশপ। মামা কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসলেন, সাথে প্রেসক্রিপশনের ওষুধ। একটা ওষুধ খুব দামী, প্রতিটি দুশো টাকা। আমি জানি না ঠিক কোন অথরিটি থেকে এই ওষুধটা কোভিড রোগীদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ দিচ্ছেন। উনি সুবর্ণার কাছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। তখনও আমি খুব খারাপ অবস্থায় না।
করোনা ওয়ার্ডে সবাই করোনা রোগী। ভাবছি— আমার একার কাছ থেকে ওদের করোনা পজেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা যদি দশ হয় তাহলে দশজনের কাছ থেকে তো একশো। ঈশপ বা সুবর্ণা আর একজনের করোনা হলেই তো অবস্থা আমাদের ভয়ানক বেগতিক হয়ে যাবে। তখনও আমার অক্সিজেন লাগছে না। সুবর্ণাকে বললাম, “হাসপাতালে থাকবো না, চলো, বাসায় চলে যাই।” ভর্তি ক্যানসেল করে বাসায় চলে আসলাম। এটা ভুল ছিল। বাসায় এসে বিকালে সুবর্ণাকে ল্যাবএইডের সেই ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। ডাক্তার কভিড-১৯ পজেটিভ শুনে প্রেসক্রিপশ করে দিলো আবার। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকেও একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলো। ফ্যাপিরাপিরাভির নামে একটা এন্টি ভাইরাল ওষুধ দিয়েছিল। প্রতি পিচ দুশো টাকার দামের এই ওষুধ প্রতিদিন দুই বেলায় আটটা খেতে হবে!
ল্যাবএইডের ডাক্তার সুবর্ণাকে বলেছে, ফ্যাপিরাপিরাভির সকালে আটটা এবং রাতে আটটা খেতে, এরপর তিনটা/চারটা করে খেতে। কিন্তু প্রেসক্রিপশনে এই ওষুধের কথা কিছু লেখে নাই। তারমানে ফরিদপুরে কভিড রোগীদের এই ওষুধ দেদারচ্ছে গেলানো হচ্ছে! এটা কি ঠিক হচ্ছে? সুবর্ণাকে বললাম, “ভেরিফাই করো আরেকজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে।” কভিডের চাপ তখন সবার উপরে। সুবর্ণা আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলো। ডাক্তারের চেয়ে আমি বেশি বুঝি ইত্যাদি। সারারাত আমার ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটলো। এর আগে ঢাকা থেকে দিদারকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাতেও সুবর্ণার সমস্যা। একটা অটিস্টিক বাচ্চা নিয়ে ওর পক্ষে একা আমাকে দেখাশুনা করা সম্ভব? ঐদিন রাতে কিছু খেলাম না, সকালেও খেতে পারলাম না, দুপুরে দুএকগাল ভাত খেলাম। বিকালের দিকে অবস্থার ভয়ানক অবনতি। আবার ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে গেলাম। এদিন ভর্তিতে সমস্যা হলো না। আমি কাউকে কিছু না বলে দিদারের ঘাড়ে ভর দিয়ে বেডে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নার্সকে অক্সিজেন লাগিয়ে দিতে বললাম। অক্সিজেন স্যাচুরেশন তখন ৯২ দেখাচ্ছে।
সুবর্ণাকে বললাম একগ্লাস হরলিকস্ গুলে দিতে। একটা ডাব আনতে বললাম। একটা হাফ বয়েল ডিম গালের মধ্যে ছেড়ে দিতে বললাম। এইটুকু না খেলে ঐদির রাতেই বোধহয় আমি মারা যেতাম। তারপরও মধ্যরাতে আমার পালস্ পাওয়া যাচ্ছে না, গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কর্তব্যরত নার্স ডিউটি ডক্টরকে জানালেন। কিন্তু ডাক্তার কেউ আসলেন না। নার্স দিদারকে বললেন, ডাক্তার বলেছে ইসিজি করাতে, কিন্তু আমাদের এখানে দিনে ছাড়া ইসিজি করানোর ব্যবস্থা নেই। আমি তখন কথা বলতে পারছি না, কিন্তু কানে শুনতে পারছি। আমি ধীরে ধীরে হাত নাড়ায়ে বুঝলাম যে, মরি নাই। সাজ্জাদ ভাই এবং লক্ষ্মী ভাবী ঐ রাতেই হাজির হলেন। সাজ্জাদ ভাই বাইরে থেকে ইসিজি মেশিন আনিয়ে ইসিজি করালেন। দেখা গেলো— আমি বেঁচে আছি। শ্বাস:কষ্ট বেড়েছে। ডাক্তার তখন কী ব্যবস্থাপত্র দিলো মনে নেই। আমি এরপর ঘুমিয়ে গেছিলাম। অক্সিজেন মাস্কটাই তখন সম্বল। সচেতনভাবে শুয়ে থাকলাম যাতে মাস্ক খুলে না যায়। সুবর্ণাকে গা হাত পা একটু ম্যাসেজ করে দিতে বলেছিলাম ইঙ্গিতে। কথা গলা থেকে বেরোচ্ছিল না।
সকালে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে, আমাকে ঢাকায় নেবে নাকি এখানেই রাখবে। ডাক্তার বলছে, ঢাকায় নিলে ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত আমি ঢাকায় ট্রান্সফার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির এবং সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুলকে জানানো হলো। ওনারা তখনও বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়ে পারেননি, কারণ, কভিড-১৯ পজেটিভ কারও হতেই পারে, হচ্ছেই। জানানোর মধ্যে কিছুটা গলদও ছিলো।
সুবর্ণাকে বললাম গোপালগঞ্জের ডিসি শাহিদা আপাকে একটা ফোন করতে। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল ঢাকায় গিয়ে কোনো হাসপাতালে সিট পাওয়া যাবে না। শাহিদা আপা ঢাকা মেডিকেলে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু কার্যত ঢাকা মেডিকেলে সিট ছিল না।
অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার সময় ক্যানোলা খুলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরা শুরু হলো। সেটি নিয়েও ওদের ভয়। হেক্সিসল দিয়ে মুছে তুলা দিয়ে চেপে ধরে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর রক্ত পড়া বন্ধ হলো। আমার সমস্যা তখন শ্বাস:কষ্ট, আমি এক মিনিটের জন্যও অক্সিজেন মাস্ক খুলছি না। দুই পায়ে বল নেই। ওদের ঘাড়ে ভর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠলাম। হঠাত মনে হলো একটা অক্সিজেনে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছুনে যাবে না। অক্সিজেন অনেক বেশিও লাগতে পারে। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে আরেকটা অক্সিজেন নিতে বললাম। পরে দাদাবাবুও অক্সিজেনের বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দিয়েছে। ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় আমার ততপরতা দেখে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারও খুব ততপর হলেন। বিমানের মতো অ্যাম্বুলেন্স চলছে। সব গাড়ী পিছনে পড়ে যাচ্ছে। গাছপালা ঘরবাড়ী সব উড়ে উড়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছে।
পথে ওদের বললাম, আমাকে একটা কলা খাওয়াতে। পথ থেকে একটা কলা কিনে খাইলাম। আরিচা ফেরিতে পৌঁছে শ্বা:সকষ্ট বেড়ে গেলো। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে অক্সিজেন সর্বোচ্চ লিমিটে দিতে বললাম। ফেরির সময়টুকুতে আমার ভয়ানক খারাপ অবস্থা হলো। অ্যাম্বুলেন্স যখন চলছিল তখন বাইরের বাতাসটা খুব কাজে দিচ্ছিল। এদিকে ঈশপ বমি শুরু করলো। সুবর্ণার অবস্থা তখন ভয়ানক। ঈশপ যখন বমি করছে ও তখন আসলেই ভেঙে পড়েছে। আমি ওকে হাত দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, ঈশপ বমি করছে অ্যাম্বুলেন্সের ঝাঁকুনির কারণে, অন্যকিছু না। ওকে কিছু খাওয়ায়। আমি নিজে ফেরি থেকে ডাব খাইলাম। ভুল হয়েছিল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ক্যাথেটার না লাগিয়ে। নিচের অংশ অবস হয়ে গেছে যেন, কিছুতেই প্রস্রাব করতে পারছিলাম না। অবশেষে সুবর্ণার সহযোগিতায় বোতলে কিছুটা করা গেলো, তারপরও পেট ফুলে থাকলো।
হঠাত করে শরীরে ছটফটানি শুরু হলো। যাই যাই অবস্থা, খিঁচুনি টাইপের। অ্যাম্বুলেন্স থামাতে বললাম। ঝাঁকুনি সহ্য হচ্ছে না। একটু বসার চেষ্টা করে আবার পড়ে গেলাম। খানিকটা সেন্সলেস বলা চলে তখন, কানে শুধু কিছু শব্দ আসছে ওদের কথা কিছু বুঝতে পারছি না। ঘণ্টাখানেক পরে অবস্থার আবার একটু উন্নতি হলো।
ঢাকা মেডিকেলের সামনে গেলে দাদা বাবু রিসিভ করলেন। উনি নরম শরম ভালো মানুষ, তাছাড়া সরকারি হাসপাতালে ওনার চিকিতসা করানোর অভিজ্ঞতা কম, তারপরও ওনার মতো করে উনি চেষ্টা করেছেন। টাকা পয়শা খরচ করেছেন। কিন্তু সিট যে নেই এটা বুঝতে লেগেছে আধা ঘণ্টা, তাও হুইল চেয়ারে আমাকে উপরে নেওয়ার পর। সেখানে হুইল চেয়ার ঘুরায়ে ঘুরায়ে খানিকক্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নামিয়ে আবার আমাক অ্যাম্বুলেন্সে উঠালো। অ্যাম্বুলেন্স আবার রাস্তায়। আমি মুকুল ভাইয়ের ফোন নম্বর বের করে দিদারকে ফোন দিতে বললাম। এর আগে ডাক্তার মামুন আল মাহতাব ভাইকে ফোন দেওয়া হয়েছে। তিনি চেষ্টা করছেন। অ্যাম্বুলেন্সও থেমে নেই, অ্যাম্বুলেন্স কুর্মিটোলা হাসপাতালের দিকে ছুটছে, ততক্ষণে মুকুল ভাই সোহরোওয়ার্দী হাসপাতালে সিট ম্যানেজ করেছেন।
সোহরাওয়ার্দীতে কভিডের ট্রিটমেন্ট ভালো দেখলাম। রোগীরা ভালোই সেবা পাচ্ছেন। এরকম দেশে কিছু সমস্যা থাকবেই, সেগুলো মেনে নিয়ে ভালোই বলা যায়। এটা ডাক্তার উত্তর বড়ুয়ার অবদান। তিনি সোহারাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ অনেক কিছুই ভালো করে গিয়েছেন। তবে সকালের নাস্তার কলা এরং আপেলটা খাওয়ার জন্য দিলে ভালো হয়। খেতে হলে আরেকটু ভালো লাগবে।
যেকোনো সরকারি হাসপাতালে নিচে হুইল চেয়ার এবং স্ট্রেচার থাকে না, তখন আয়া বুয়া বা ওয়ার্ড বয়রা জিম্মি করে, এই নাটকে মিনিট দশেক নষ্ট হয়। রোগীদের জন্য নিচে দশটা হুইল চেয়ার এবং স্ট্রেচার থাকলে তো এমার্জেন্সি মুহূর্তে রোগীর স্বজনরাও হাত লাগাতে পারে। আয়া বুয়া এবং ওয়ার্ড বয়দের এই ক্ষমতার একটা উতস হতে পারে যে, তারা বেশ কিছু টাকা দিয়ে এই পোস্টে ঢোকে ফলে কর্তৃপক্ষ হয়ত ওদের এই ছাড়গুলো দিতে বাধ্য হয়। হয়ত।
অক্সিজেন অক্সিজেন অক্সিজেন, অক্সিজেন সেই লাগানো তো লাগানোই আছে। জাস্ট গাড়ীর অক্সিজেনটা খুলে হাসপাতালের অক্সিজেন। শেষপর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের দুই তলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩ নম্বর বেড আমার ঠিকানা হলো। অক্সিজেন পেলাম। কিছুটা মানসিক তৃপ্তি হলো, চিকিতসা তখনও অনেক দূরের বিষয়। চিকিতসা কিছু আসলে নেইও। দমটা (আত্মবিশ্বাসটা) ধরে রাখা, অক্সিজেনটা চালিয়ে যাওয়া, পেটে কিছু পুষ্টিকর খাবার দাওয়া, আর কিছু ওষুধু টষুধ তো থাকেই।
এরপর তো অনেকেই আমার জন্য সোহরাওয়াদীতে সুপারিশ করেছেন, মুকুল ভাই, ডা: মামুন আল মাহতাব ভাই, শাহিদা আপা সুপারিশ করেছেন, তাতে কাজ হয়েছে, সেবার মান বেড়েছে। মুকুল ভাই সবসময় আপডেট নিয়েছেন। ডা: সুজন, ডা: মাসুদ নামগুলো মনে থাকবে। তবে একটা গণ জায়গায় গিয়ে আমি কখনও এক্সট্রা সুবিধা নিতে চাই না। সবাই যেটা পাচ্ছে ওটাই যথেষ্ট। ফলে ওয়ার্ডে বাকী রোগীরাও ছিলেন আমার অক্সিজেন, সবাইকে দেখে সাহস এবং স্বস্তি পাচ্ছিলাম। কিন্তু শরীর আর সাড়া দিতে পারছিলো না। সোহরাওয়াদীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাতটা ছিল আমার জন্য ভয়ঙ্কর। ভয় কাটতে শুরু করেছিল তৃতীয় দিন থেকে।
-চলবে