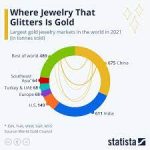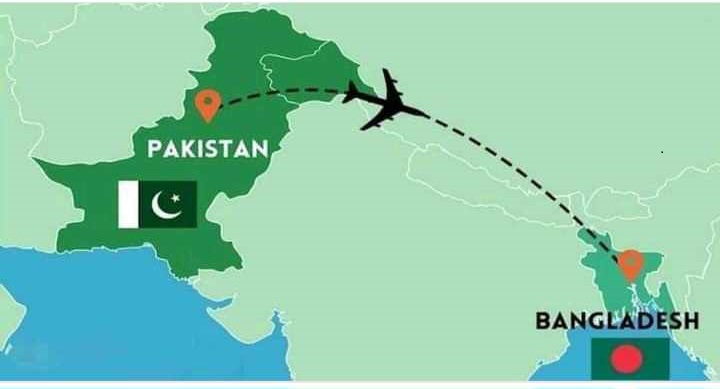এটি একটি দৃশ্যপ্রধান চলচ্চিত্র। প্রধানত গ্রাম, এবং শহরের প্রচুর দৃশ্য চিত্রায়ন করা হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। বিশেষত নিম্নবিত্ত এবং বৈষম্যের ধাক্কায় ছিটকে পড়া মানুষের জীবন, জীবনের সংগ্রাম এবং নিগ্রহের দিকটি উঠে এসেছে। নির্মাতা লতা আহমেদ কাজটি করেছেন সুনিপুনতায়, সহজ সরল স্বাভাবিকভাবে মৃৎসন্তান হয়ে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য দরদ ঢেলে দিয়ে। এক কথায় চলচ্চিত্রটি হচ্ছে নির্মাতার শিল্পীত মন এবং সুদৃঢ় মানব প্রেমের অকপট বহিঃপ্রকাশ। চিত্রায়নের প্রতি পদে পদে প্রকাশ পেয়েছে, শ্রেষ্ঠাংশেও লুকায়িত থাকেনি নির্মাতার বৈষম্যহীন সমাজ আকাঙক্ষার বিষয়টি।
যেহেতু দৃশ্যপট বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাজটি করা হয়েছে সংলাপ ব্যতীরেখে, তাই এটি দর্শকের কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। গ্রামবাংলার যে দৃশ্যগুলো এখনে তুলে আনা হয়েছে সেগুলো চিরায়ত বাংলার এক ঐতিহাসিক দলিল— এর আগে এতটা প্রায়োগিকভাবে কেউ তুলে আনেনি বাংলার মানুষের লোকায়ত জীবন, যে জীবন আমরা দেখি রোজ কিন্তু কোথাও তা আখ্যান হিসেবে উপস্থিত হয়নি হাল আমলের চলচ্চিত্র বা উপন্যাসে। সেদিক থেকে লতা আহমেদের ‘সোহাগীর গয়না’ চলচ্চিত্রটি অবশ্যই ব্যতিক্রম। বাংলা এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রধানত একটি গ্রাম প্রধান অঞ্চলই ছিল, এখনো তাই। গ্রামের মানুষের অভাব অনটন যেমন ছিল আবার এক ধরনের প্রাকৃতিক লোকায়ত জীবনও ছিল, সে জীবন যে শুধু দুঃখেরই ছিল —এমনটা ভাবা মোটেও সমীচীন নয়। অভাব অনাটন এবং দুঃখের আড়ালে সুলভ কিছু সুখের নাগাল গ্রামের মানুষে তখন পেত। লতা আহমেদ মানুষের মৃৎগত সে জীবন ধারণ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করেছেন নিশ্চয়ই তিনি সে জীবনের সাথে ঘনিষ্ট বলেই, এবং তাদের অন্তরে ধারণ করেছেন বলেই তিনি তা করতে পেরেছেন সফলভাবে।
চলচ্চিত্রটিতে খুব সুক্ষ্মভাবে আবশ্যিক কিছু বিষয় নির্দেশনা হিসেবে রয়েছে। রাজা যখন সুর করে “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি …” পড়তে থাকে তখন তার ‘সৎ’ বাবা এসে পিদিম নিভিয়ে দেয়। তখন রাজার মা আক্ষেপ করে বলে, তোর পড়াশুনার জন্য এই নিকাহ্ করছিলাম।” এখানে নারীর দ্বিতীয় বিয়ের স্বীকৃতি যেমন রয়েছে, একইসাথে উপার্জন এবং কর্মের স্বীকৃতি বঞ্চিত নারীর আক্ষেপের বিষয়টিও রয়েছে। নির্মাতা এখানে রাজাকে দিয়ে যে ছড়াটি পড়িয়েছেন সেখানেও তিনি চিন্তার খোরাক রেখেছেন— পূর্বে আমাদের পাঠপরিকল্পনায় নৈতিক শিক্ষায় দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত, “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি …” ছড়াটির মধ্য দিয়ে নির্মাতা সেটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন। রাজা যখন খেলতে গিয়ে পড়ে যায় এবং হাটু ছিলে যায় তখন তার বোন সোহাগী রাজার হাটুতে দুর্বা চাবায়ে লাগিয়ে দেয়। এখানে আমাদের প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসার দিকটি উঠে এসেছে। রয়েছে প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের বিষয়টিও— রাজাকে সানকিতে কয়েক ধরনের ভর্তা নিয়ে খেতে দেখা যায়। মুড়ি ভাজার দৃশ্যটিতে বাঙালির অকৃত্রিম খাদ্যাভ্যাসের দিকটি আরও জোরালোভাবে ফুঁটে উঠেছে।
চলচ্চিত্রটিতে এমন কিছু গ্রামীণ দৃশ্যপট রয়েছে, যা এক সময় পৃথিবীর কোথাও হয়ত আর থাকবে না। তাই ইতিহাস সংরক্ষণের দিক থেকেও চলচ্চিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। বালিকচায় (কাঠের একটি চিকন ফালি) বালি লাগিয়ে ছুরিতে ধার দেওয়া বাংলার একটি চিরায়ত দৃশ্য ছিল। তালগাছ এবং খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে ধারালো ছুরির প্রয়োজন হয়, সেজন্যই এভাবে ধার দেওয়া হত । খেজুর গাছে রস পাড়তে ওঠার সময় গাছে কুর্নিশ করে ওঠার বিষয়টি গ্রামবাংলার কিছু সংস্কারের বিষয় মনে করিয়ে দেয়।
পুতুল নাচ দেখা, রকমারি মেলা, ভীড় করে বসে বাউল গান শোনা, পোলো দিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি দৃশ্যগুলো গ্রামবাংলার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনেরই অংশ ছিল। গ্রামের শিশুদের রান্নাবাটি খেলার মধ্য দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামের মানুষের ভাতের কষ্টের বিষয়টি— একটি শিশু আরেকটি শিশুকে বলছে, “তুই এত ভাত ভাত করস ক্যান, জীবনে কোনোদিন ভাত খাস নাই।” শিশুটি উত্তরে বলছে, “সকালে কিছু খাই নাই, আমাগো ঘরে চাল আছিল না।” বাংলার গ্রামের মানুষের খাওয়া বলতে একসময় ভাতই বুঝানো হত। শাক সবজি মাছ তারা প্রকৃতি থেকেই পেত, ফলে খাওয়ার কষ্ট বলতে একসময় ভাতের কষ্টই বুঝাত— বিষটি এখানে শিশুদের খেলার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।
গ্রামের মানুষের প্রকৃতি নির্ভর জীবন ও জীবীকার চমৎকার দৃশ্যায়ন এ চলচ্চিত্রটি। গ্রামের একজন কুমোর কয়েকটি পুতুল নিয়ে বসে আছে বিক্রির আশায়, আপন মনে পুতুলে রং করছে— গ্রামে এমন কিছু মানুষ সবসময় থাকত যারা উপার্জনকে প্রধান না ভেবে তারা শখের কাজটিকে কোনোমতে টিকে থাকার অবলম্বন করে বাঁচতে চাইত। পতুলের কারিগর এ কুমোরটি সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। সোহাগীদের পুতুলের শখ থাকলেও একটি পুতুল কিনে নেওয়ার সামার্থ তাদের নেই, সে একটি পুরোনো পুতুল কুড়িয়ে নেয়, কুমোরের কাছ থেকে তুলি নিয়ে তাতে রং-এর ফোঁটা কাটে।
গ্রাম বাংলার নান্দনিক এবং জীবনবাস্তবিক এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে খানিকটা এগঘেয়েমি আসাটা স্বাভাবিক। মনোটনি দূর হবে রাজার হঠাৎ ঢাকা যাত্রার মধ্য দিয়ে। রাজা ঢাকায় চলে আসে পিতার অত্যাচার সইতে না পেরে। লঞ্চের টিকিট না কাটায় নামার সময় চেকারের হাতে থাপ্পড় খাওয়া থেকে শুরু হয় রাজার সংগ্রামী জীবন। ঢাকায় রাজার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে বৈষম্যে পদপিষ্ঠ মানুষের জীবন, সে জীবন গ্রামের চেয়ে ভিন্ন, কঠোর এবং কঠিন। বাসাবাড়ির ময়লা টেনে জীবীকা নির্বাহ করা মাণিক এবং তার ছোট ভাইয়ের জীবনটা হৃদয়গ্রাহী। আবর্জনার মধ্যে মাণিক একটি পুটলি পায়, তাতে ছিল কিছু টাকা এবং সোনার গয়না, মাণিকদের মা সেগুলো নিয়ে এক ব্যাটার সাথে চলে যায়। ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব বর্তায় মাণিকের ওপর। রাজার বেঁচে থাকার শুরুটাও এই নর্দমাক্ত জীবনের মধ্য দিয়ে। আবর্জনার মধ্যে এক প্যাকেট পাওরুটি পেয়ে খুলে খেয়ে নেয় রাজা— দৃশ্যটি মানুষের ক্ষুধা নিবৃতির চরম বাধ্যবাধকতারই করুণ দৃশ্যায়ন।
রাজা ধীরে ধীরে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হতে থাকে। আবর্জনা কুড়ানো, রেস্টুরেন্টের থালা বাসন মাজা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে করতে হাতে কিছু টাকা পেয়ে একদিন সে তা রাস্তার ধারে বসে গুণতেছিল। হঠাৎ পুলিশ এসে রাজাকে গাড়িতে তুলে নেয়। কিছুদূর নিয়ে গিয়ে টাকা রেখে আবার রাস্তায় ফেলে দেয়। এটি ঢাকা শহরের রাস্তাকে আপন করে বেঁচে থাকা মানুষের নৈমিত্তিক আপদ। এরপর রাজা কাজ নেয় একটি ওয়ার্কশপে। কাজ শিখতে শিখতে তার কাজের গতি বাড়ে। এক সময় তার হাতে কিছু টাকা জমে। টাকা দিয়ে সে তার বোন সোহাগীর জন্য গয়না কেনে। গয়না নিয়ে বাড়ি ফেরে, ফেরার পথে নদী ভাঙনের চিত্র এবং জোড়াতালি দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দর্শকদের ব্যথিত এবং বিস্মিত করে নিশ্চয়ই। ফিরে গিয়ে রাজা বাড়িটি আর পায় না। বাড়িটি কিনে নিয়েছে প্রবাসী একজন, রাজার পরিবার চলে গিয়েছে অন্যত্র।
চলচ্চিত্রটি ছোটগল্পের মতো “শেষ হইয়াও হইল না শেষ” ধরনের— রাজার জীবনালেখ্য আরেকটু দেখার অপেক্ষা নিয়ে দর্শক মনে মনে নিশ্চয়ই বলে, নির্মাতা হয়ত এই চলচ্চিত্রটির ধারাবাহিকতায় আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন, যেখানে রাজার জীবনের দ্বিতীয় পাঠ দর্শক দেখতে পাবে, উঠে আসবে শ্রেণি সংগ্রামের নতুন কোনো দিক।